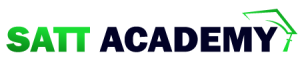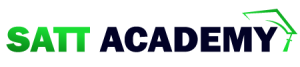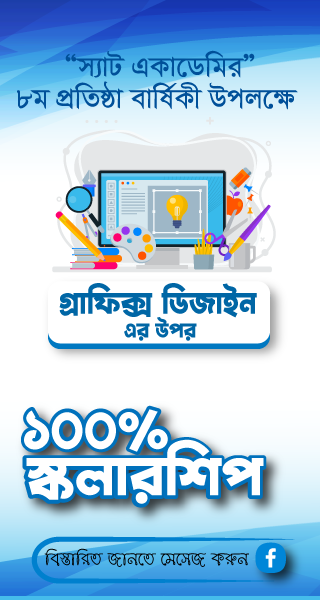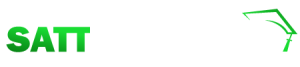আদিম যুগের মানুষ কৃষিকাজ জানত না। বনে বনে ঘুরে ফলমূল সংগ্রহ করত। তা-ই ছিল তাদের খাদ্য । এরপর মানুষ পাথর ভেঙে ঘষে ঘষে ধারালো অস্ত্র তৈরি করতে শেখে। সে সময় পাথরই ছিল তাদের একমাত্র হাতিয়ার । সে কারণে এ যুগকে পাথরের যুগ বলা হতো। পাথর যুগের প্রথম পর্যায়কে বলা হতো পুরনো পাথরের যুগ বা পুরোপলীয় যুগ । এ যুগে মানুষ পাথরের অস্ত্র দিয়ে দলবদ্ধভাবে পশু শিকার করত । এরা আগুনের ব্যবহারও জানত । পুরনো পাথরের যুগ শেষ হয় মানুষের যাযাবর জীবনের অবসান ঘটিয়ে কৃষিভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে । এ যুগকে বলা হয় নতুন পাথরের যুগ বা নবোপলীয় যুগ। কৃষির প্রয়োজনে এ যুগে মানুষ নদীর তীরে বসবাস শুরু করে । ঘর-বাড়ি নির্মাণ করতে শেখে । এভাবেই মানবসভ্যতার শুরু। এই অধ্যায়ে কীভাবে মানুষ ধাপে ধাপে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে তারই সত্য কাহিনি, যাকে আমরা বলি ইতিহাস— সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে।
এই অধ্যায় শেষে আমরা -
♦ প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণনা করতে পারব;
♦ নীল নদের অবদান উল্লেখপূর্বক প্রাচীন মিশরের রাষ্ট্র ও সমাজের বর্ণনা করতে পারব; বিশ্বসভ্যতা বিকাশে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অবদানসমূহ মূল্যায়ন করতে পারব;
♦ সিন্ধুসভ্যতা আবিষ্কারের কাহিনি ও ভৌগোলিক অবস্থান জানতে পারব;
♦ সিন্ধুসভ্যতার রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা করতে পারব;
♦ সভ্যতার বিকাশে সিন্ধুসভ্যতার নগর পরিকল্পনা, শিল্পকলা ও ভাস্কর্যের বর্ণনা করতে পারব;
♦ ভৌগোলিক অবস্থান ও সময়কালের বর্ণনাপূর্বক গ্রিক সভ্যতার উদ্ভবের পটভূমি বর্ণনা করতে পারব;
♦ নগররাষ্ট্রের ধারণা প্রদানপূর্বক গণতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব;
♦ বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতিতে গ্রিকসভ্যতার শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের অবদান বর্ণনা করতে পারব;
♦ ভৌগোলিক অবস্থান ও সময়কাল উল্লেখপূর্বক প্রাচীন রোমান সভ্যতা বর্ণনা করতে পারব;
♦ রোম নগরী ও রোমান শাসনের বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব;
♦ শিক্ষা, সাহিত্য ও লিখন পদ্ধতির বিকাশে প্রাচীন রোমান সভ্যতার অবদান বিশ্লেষণ করতে পারব; সভ্যতার বিকাশে প্রাচীন রোমান সভ্যতার স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও বিজ্ঞানের অবদান বর্ণনা করতে পারব;
♦ বিশ্বসভ্যতায় প্রাচীন রোমান সভ্যতার ধর্ম, দর্শন ও আইনের প্রভাব আলোচনা করতে পারব;
♦ বিশ্বসভ্যতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের মাধ্যমে প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব ।
২৩টি
২৪টি
২৫টি
২৬টি
পটভূমি: আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে অবস্থিত দেশটির নাম ইজিপ্ট বা মিশর । খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ থেকে ৩২০০ অব্দ পর্যন্ত নীল নদের অববাহিকায় একটি সমৃদ্ধ জনপদের উদ্ভব হয়। এ সময় থেকে মিশর প্রাচীন সভ্যতায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে শুরু করে। যেমন : ৩২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে প্রথম রাজবংশের শাসন আমল শুরু হয়। এ সময় থেকে মিশরের ঐতিহাসিক যুগের সূচনা হয় । একই সময়ে নারমার বা মেনেস হন একাধারে মিশরের প্রথম নরপতি এবং পুরোহিত। তিনি প্রথম ফারাও-এর মর্যাদাও লাভ করেন। এরপর থেকে ফারাওদের অধীনে মিশর প্রাচীন বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতিতে একের পর এক উল্লেযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয় ।
ভৌগোলিক অবস্থান: তিনটি মহাদেশ দ্বারা ঘিরে থাকা মিশরের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশটি এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত । এর উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পূর্বে লোহিত সাগর, পশ্চিমে সাহারা মরুভূমি, দক্ষিণে সুদান ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশ । এর মোট আয়তন প্রায় চার লক্ষ বর্গমাইল ।
সময়কাল: মিশরীয় সভ্যতা ২৫০০ বছরেরও বেশি সময়ব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল। প্রাচীন মিশরের নিরবচ্ছিন্ন ও দীর্ঘ ইতিহাসের সূচনা হয় ৫০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। বিশেষ করে নবোপলীয় যুগে । তবে মিশরীয় সভ্যতার গোড়াপত্তন হয় মেনেসের নেতৃত্বে, যা প্রায় তিন হাজার বছর ধরে স্বমহিমায় উজ্জ্বল ছিল । খ্রিষ্টপূর্ব দশম শতকে লিবিয়ার এক বর্বর জাতি ফারাওদের সিংহাসন দখল করে নেয় । ৬৭০-৬৬২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে অ্যাসিরীয়রা মিশরে আধিপত্য বিস্তার করে । ৫২৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পারস্য মিশর দখল করে নিলে প্রাচীন মিশরের সভ্যতার সূর্য অস্তমিত হয় ।
রাষ্ট্র ও সমাজ: প্রাক-রাজবংশীয় যুগে মিশর কতকগুলো ছোট নগর রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এগুলোকে ‘নোম’ বলা হতো । মিশরের প্রথম রাজা বা ফারাও (মেনেস বা নারমার) সমগ্র মিশরকে খ্রিষ্টপূর্ব ৩২০০ অব্দে ঐক্যবদ্ধ করে একটি রাজ্য গড়ে তোলেন, যার রাজধানী ছিল দক্ষিণ মিশরের মেম্ফিসে । তখন থেকে মিশরে ঐক্যবদ্ধ রাজ্য ও রাজবংশের উদ্ভব। মিশরীয় ‘পের-ও' শব্দ থেকে ফারাও শব্দের জন্ম। ফারাওরা ছিল অত্যন্ত ক্ষমতাশালী । তারা নিজেদের সূর্য দেবতার বংশধর মনে করত। ফারাও পদটি ছিল বংশানুক্রমিক । অর্থাৎ ফারাওয়ের ছেলে হতো উত্তরাধিকার সূত্রে ফারাও । পেশার ওপর ভিত্তি করে মিশরীয়দের কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন— রাজপরিবার, পুরোহিত, অভিজাত, লিপিকার, ব্যবসায়ী, শিল্পী এবং কৃষক ও ভূমিদাস শ্রেণি ।
মিশরের অর্থনীতি মূলত ছিল কৃষিনির্ভর। উৎপাদিত ফসলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গম, যব, তুলা, পেঁয়াজ, পিচফল ইত্যাদি। ব্যবসা-বাণিজ্যেও মিশর ছিল অগ্রগামী। মিশরে উৎপাদিত গম, লিনেন কাপড় ও মাটির পাত্র ক্রিট দ্বীপ, ফিনিশিয়া, ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় রপ্তানি হতো । বিভিন্ন দেশ থেকে মিশরীয়রা স্বর্ণ, রৌপ্য, হাতির দাঁত, কাঠ ইত্যাদি আমদানি করত ।
নীল নদ: মিশরের নীল নদের উৎপত্তি আফ্রিকার লেক ভিক্টোরিয়া থেকে । সেখান থেকে নদটি নানা দেশ হয়ে মিশরের মধ্য দিয়ে ভূ-মধ্যসাগরে এসে পড়েছে । ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস যথার্থই বলেছেন- 'মিশর নীল নদের দান'। নীল নদ না থাকলে মিশর মরুভূমিতে পরিণত হতো । প্রাচীনকালে প্রতিবছর নীল নদে বন্যা হতো। বন্যার পর পানি সরে গেলে দুই তীরে পলিমাটি পড়ে জমি উর্বর হতো। জমে থাকা পলিমাটিতে জন্মাতো নানা ধরনের ফসল ।
সভ্যতায় মিশরীয়দের অবদান: প্রাচীন সভ্যতায় মিশরীয়দের অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই । ধর্মীয় চিন্তা, শিল্প, ভাস্কর্য, লিখন পদ্ধতি, কাগজের আবিষ্কার, জ্ঞান বিজ্ঞানচর্চা—সবকিছুই তাদের অবদানে সমৃদ্ধ। মিশরীয়দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তাদের জীবন ধর্মীয় চিন্তা ও বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত ছিল।
মিশরীয়দের ধর্মবিশ্বাস: সম্ভবত প্রাচীন মিশরীয়দের মতো অন্য কোনো জাতি জীবনের সকল ক্ষেত্রে এতটা ধর্মীয় নিয়ম-কানুন অনুশাসন দ্বারা প্রভাবিত ছিল না। সে কারণে মানবসভ্যতার অনেক ধ্যানধারণা, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানের জন্ম প্রাচীন মিশরে । তারা জড়বস্তুর পূজা করত, মূর্তি পূজা করত, আবার জীবজন্তুর পূজাও করত। বিভিন্ন সময়ে তাদের ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটেছে। মিশরীয়দের ধারণা ছিল- সূর্যদেবতা ‘রে’ বা ‘আমন রে’ এবং প্রাকৃতিক শক্তি, শস্য ও নীল নদের দেবতা ‘ওসিরিস’ মিলিতভাবে সমগ্র পৃথিবী পরিচালিত করেন । তবে, তাদের জীবনে সূর্যদেবতা ‘রে’- এর গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি । মিশরীয়রা মনে করত মৃত ব্যক্তি আবার একদিন বেঁচে উঠবে । সে কারণে দেহকে তাজা রাখার জন্য তারা মমি করে রাখত । এই চিন্তা থেকে মমিকে রক্ষার জন্য তারা পিরামিড তৈরি করেছিল। ফারাওরা স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে দেশ শাসন করত। তারা ছিল প্রধান পুরোহিত এবং অন্যান্য পুরোহিতকেও তারা নিয়োগ করত ।
শিল্প : মিশরীয়দের চিত্রকলা বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ । অন্যান্য দেশের মতো চিত্রশিল্পও গড়ে উঠেছিল ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে । তারা সমাধি আর মন্দিরের দেয়াল সাজাতে গিয়ে চিত্রশিল্পের সূচনা করে । তাদের প্রিয় রং ছিল সাদা-কালো। সমাধি, পিরামিড, মন্দির, প্রাসাদ, প্রমোদ কানন, সাধারণ ঘর-বাড়ির দেয়ালে মিশরীয় চিত্রশিল্পীরা অসাধারণ ছবি এঁকেছেন । সেসব ছবির মধ্যে সমসাময়িক মিশরের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের কাহিনি ফুটে উঠেছে । কারুশিল্পেও প্রাচীন মিশরীয় শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। আসবাবপত্র, মৃৎপাত্র, সোনা, রুপা, মূল্যবান পাথরে খচিত তৈজসপত্র, অলঙ্কার, মমির মুখোশ, দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র, হাতির দাঁত ও ধাতুর দ্রব্যাদি মিশরীয় কারু শিল্পের দক্ষতার প্রমাণ বহন করে ।
ভাস্কর্য: ভাস্কর্য শিল্পে মিশরীয়দের মতো প্রতিভার ছাপ আর কেউ রাখতে সক্ষম হয়নি। ব্যাপকতা, বৈচিত্র্য এবং ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত বিশাল আকারের পাথরের মূর্তিগুলো ভাস্কর্য শিল্পে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। প্রতিটি ভাস্কর্য ধর্মীয় ভাবধারা, আচার অনুষ্ঠান, মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। প্রতিটি শিল্পই ছিল আসলে ধর্মীয় শিল্পকলা। সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য হচ্ছে গিজার অতুলনীয় স্ফিংক্স। স্ফিংক্স হচ্ছে এমন একটি মূর্তি, যার দেহ সিংহের মতো, কিন্তু মুখ মানুষের মতো। মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিড হচ্ছে ফারাও খুফুর পিরামিড । মন্দিরগুলোতে মিশরীয় ভাস্কর্য স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে।
লিখনপদ্ধতি ও কাগজ আবিষ্কার: মিশরীয় সভ্যতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল লিপি বা অক্ষর আবিষ্কার । নগর সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মিশরীয় লিখনপদ্ধতির উদ্ভব ঘটে । পাঁচ হাজার বছর পূর্বে তারা সর্বপ্রথম ২৪টি ব্যঞ্জনবর্ণের বর্ণমালা আবিষ্কার করে । প্রথম দিকে ছবি এঁকে তারা মনের ভাব প্রকাশ করত । এই লিখন পদ্ধতির নাম ছিল চিত্রলিপি । এই চিত্রলিপিকে বলা হয় ‘হায়ারোগ্লিফিক ’ বা পবিত্র অক্ষর । মিশরীয়রা নলখাগড়া জাতীয় গাছের কাণ্ড থেকে কাগজ বানাতে শেখে । সেই কাগজের ওপর তারা লিখত । গ্রিকরা এই কাগজের নাম দেয় 'প্যাপিরাস'। এই শব্দ থেকে ইংরেজি পেপার শব্দের উৎপত্তি। এখানে উল্লেখ্য, নেপোলিয়ান বোনাপার্টের মিশর জয়ের সময় একটি পাথর আবিষ্কৃত হয় যা রসেটা স্টোন নামে পরিচিত । যাতে গ্রিক এবং‘হায়ারোগ্লিফিক ' ভাষায় অনেক লেখা ছিল, যা থেকে প্রাচীন মিশরের অনেক তথ্য জানা যায় ।
বিজ্ঞান : মিশরীয় সভ্যতা ছিল কৃষিনির্ভর । সে কারণে নীল নদের প্লাবন, নাব্য, পানিপ্রবাহের মাপ জোয়ার-ভাটা ইত্যাদি ছাড়াও জমির মাপ তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। এসবের সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্র ও অঙ্কশাস্ত্রের ছিল গভীর যোগাযোগ । ফলে এ দুইটি বিদ্যা তারা আয়ত্ত করেছিল প্রয়োজনের তাগিদে । তারা অঙ্কশাস্ত্রের দুইটি শাখা জ্যামিতি এবং পাটিগণিতেরও প্রচলন করে । মিশরীয় সভ্যতার মানুষ যোগ, বিয়োগ ও ভাগের ব্যবহার জানত। ৪২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ তারা প্রথম সৌর পঞ্জিকা আবিষ্কার করে । ৩৬৫ দিনে বছর এ হিসাবের আবিষ্কারকও তারা। প্রাচীন মিশরের অধিবাসীরা সময় নির্ধারণের জন্য সূর্যঘড়ি, ছায়াঘড়ি, জলঘড়ি আবিষ্কার করে ।
ধর্মের কারণে মিশরীয়রা বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহী ছিল । তারা পরলোকে বিশ্বাস করত এবং ফারাওরা পরবর্তী জন্মেও রাজা হবেন এই বিশ্বাস তাদের ছিল । তাই তারা ফারাওদের দেহ তাজা রাখার পদ্ধতি আবিষ্কার করে। এ কারণেই মমি তৈরি শুরু হয় । মিশরীয় বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মৃতদেহ পচন থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন।
চিকিৎসাশাস্ত্রেও প্রাচীন মিশরীয়রা বিশেষ অগ্রগতি লাভ করেছিল । তারা চোখ, দাঁত, পেটের রোগ নির্ণয় করতে জানত । অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চিকিৎসা করার বিদ্যাও তাদের জানা ছিল । তারা হাড় জোড়া লাগানো, হৃৎপিণ্ডের গতি এবং নাড়ির স্পন্দন নির্ণয় করতে পারত ।
মিশরীয়রা দর্শন ও সাহিত্যচর্চা করত । তাদের রচনায় দুঃখ-হতাশার কোনো প্রকাশ ছিল না। তারা আশাবাদী ছিল। তাদের লেখায় সব সময়ই আনন্দের প্রকাশ দেখা গেছে ।
পটভূমি : সিন্ধু নদের অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল বলে এই সভ্যতার নাম রাখা হয় সিন্ধুসভ্যতা। সিন্ধু সভ্যতার সংস্কৃতিকে অনেক সময়ে হরপ্পা সংস্কৃতি বা হরপ্পা সভ্যতা বলা হয়ে থাকে । এই সভ্যতার আবিষ্কার কাহিনি চমৎকার । পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদারো শহরে উঁচু উঁচু মাটির ঢিবি ছিল ।
স্থানীয় লোকেরা বলত মরা মানুষের ঢিবি (মহেঞ্জোদারো কথাটির মানেও তাই) । বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপধ্যায়ের নেতৃত্বে পুরাতত্ত্ব বিভাগের লোকেরা ঐ স্থানে বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ আছে ভেবে মাটি খুঁড়তে থাকেন। অপ্রত্যাশিতভাবে বেরিয়ে আসে তাম্রযুগের নিদর্শন। একই সময়ে ১৯২২-২৩ খ্রিষ্টাব্দে দয়ারাম সাহানীর প্রচেষ্টায় পাঞ্জাবের পশ্চিম দিকে মন্টোগোমারি জেলার হরপ্পা নামক স্থানেও প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। জন মার্শালের নেতৃত্বে পুরাতত্ত্ব বিভাগ অনুসন্ধান চালিয়ে আরও বহু নিদর্শন আবিষ্কার করে।
ভৌগোলিক অবস্থান : উপমহাদেশের প্রাচীনতম সিন্ধুসভ্যতার বিস্তৃতি বিশাল এলাকা জুড়ে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে এই সভ্যতার নিদর্শন সবচেয়ে বেশি আবিষ্কৃত হয়েছে। তা সত্ত্বেও ঐ সভ্যতা শুধু সিন্ধু অববাহিকা বা ঐ দুটি শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পাকিস্তানের পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ, ভারতের পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাটের বিভিন্ন অংশে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, পাঞ্জাব থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক এলাকা জুড়ে সিন্ধুসভ্যতা গড়ে উঠেছিল ।
সময়কাল : সিন্ধুসভ্যতার সময়কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে । কেউ কেউ মনে করেন, ৩৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত এ সভ্যতার উত্থান-পতনের কাল। আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, আর্য জাতির আক্রমণের ফলে খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ১৫০০ অথবা ১৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিন্ধুসভ্যতার অবসান ঘটে। তবে, মর্টিমার হুইলার মনে করেন, এই সভ্যতার সময়কাল হচ্ছে ২৫০০ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ।
রাজনৈতিক অবস্থা : সিন্ধুসভ্যতার জনগণের রাজনৈতিক জীবন ও শাসনপ্রণালি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার নগর বিন্যাস প্রায় একই রকম ছিল । এগুলোর ধ্বংসাবশেষ দেখে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় যে, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী উঁচু ভিতের উপর শহরগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল । শহরগুলোর এক পাশে উঁচু ভিত্তির উপর একটি করে নগরদুর্গ নির্মাণ করা হতো । চারদিক থাকত প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত । নগরের শাসনকর্তারা নগর দুর্গে বসবাস করতেন। প্রশাসনিক বাড়িঘরও দুর্গের মধ্যে ছিল। নগরের ছিল প্রবেশদ্বার । দুর্গ বা বিরাট অট্টালিকা দেখে মনে হয় একই ধরনের কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে নগর দুটিতে প্রচলিত ছিল। এই প্রশাসন জনগণের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করত ।
সামাজিক অবস্থা : সিন্ধুসভ্যতার যুগে মানুষ সমাজবদ্ধ পরিবেশে বসবাস করত। সেখানে একক পরিবার পদ্ধতি চালু ছিল । সিন্ধুসভ্যতার যুগে সমাজে শ্রেণিবিভাগ ছিল। সব লোক সমান সুযোগ-সুবিধা পেত না । সমাজ ধনী ও দরিদ্র দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। কৃষকরা গ্রামে বসবাস করত । শহরে ধনী এবং শ্রমিকদের জন্য আলাদা-আলাদা বাসস্থানের নিদর্শন পাওয়া গেছে ।
পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য তারা মূলত সুতা ও পশম ব্যবহার করত। সিন্ধুসভ্যতার সমাজব্যবস্থা ছিল মাতৃতান্ত্রিক । নারীরা খুবই শৌখিন ছিল । তাদের প্রিয় অলঙ্কারের মধ্যে ছিল হার, আংটি, দুল, বিছা, বাজুবন্ধ, চুড়ি, বালা, পায়ের মল ইত্যাদি। তারা নকশা করা দীর্ঘ পোশাক পরত। পুরুষরাও অলঙ্কার ব্যবহার করত।
অর্থনৈতিক অবস্থা : সিন্ধুসভ্যতার অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষিনির্ভর। তাছাড়াও অর্থনীতির আর একটি বড় দিক ছিল পশুপালন । কৃষি ও পশুপালনের পাশাপাশি মৃৎপাত্র নির্মাণ, ধাতুশিল্প, বয়নশিল্প, অলঙ্কার নির্মাণ, পাথরের কাজ ইত্যাদিতেও তারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। এই উন্নতমানের শিল্পপণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সেখানকার বণিকরা বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলত। বণিকদের সাথে আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, মধ্য এশিয়া, পারস্য, মেসোপটেমিয়া, দক্ষিণ ভারত, রাজপুতনা, গুজরাট প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল ।
ধর্মীয় অবস্থা: সিন্ধুসভ্যতায় কোনো মন্দির বা মঠের চিহ্ন পাওয়া যায়নি; যে কারণে তাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয়। তবে, তাদের মধ্যে যে ধর্মবিশ্বাস ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । মন্দির বা উপাসনা গৃহের অস্তিত্ব না থাকলেও স্থানে স্থানে অসংখ্য পোড়ামাটির নারীমূর্তি পাওয়া গেছে । ধারণা করা হয়, তারা ঐ ধরনের দেবীমূর্তির পূজা করত । সিন্ধুবাসীর মধ্যে মাতৃপূজা খুব জনপ্রিয় ছিল । তাছাড়া তারা দেব-দেবী মনে করে বৃক্ষ, পাথর, সাপ এবং পশু-পাখির উপাসনাও করত । সিন্ধুবাসী পরলোকে বিশ্বাস করত । যে কারণে কবরে মৃতের ব্যবহার করা জিনিসপত্র ও অলঙ্কার রেখে দিত ।
সিন্ধুসভ্যতার অবদান : পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সিন্ধুসভ্যতা । নিম্নে এই সভ্যতার অবদান আলোচনা করা হলো:
নগর পরিকল্পনা : সিন্ধুসভ্যতার এলাকায় যেসব শহর আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সবচেয়ে বড় শহর । ঘরবাড়ি সবই পোড়ামাটি বা রোদে পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরি । শহরগুলোর বাড়িঘরের নকশা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীরা উন্নত নগরকেন্দ্রিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল । হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নগর পরিকল্পনা একই রকম ছিল । নগরীর ভেতর দিয়ে চলে গেছে পাকা রাস্তা । রাস্তাগুলো ছিল সোজা। প্রত্যেকটি বাড়িতে খোলা জায়গা, কূপ ও স্নানাগার ছিল । জল নিষ্কাশনের জন্যে ছোট নর্দমাগুলোকে মূল নর্দমার সাথে সংযুক্ত করা হতো। রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হতো । পথের ধারে ছিল সারিবদ্ধ ল্যাম্পপোস্ট ।
পরিমাপ পদ্ধতি : সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীরা দ্রব্যের ওজন পরিমাপ করতে শিখেছিল । তাদের এই পরিমাপ পদ্ধতির আবিষ্কার সভ্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে বিবেচিত । তারা বিভিন্ন দ্রব্য ওজনের জন্য নানা মাপের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির বাটখারা ব্যবহার করত । দাগ কাটা স্কেল দিয়ে দৈর্ঘ্য মাপার পদ্ধতিও তাদের জানা ছিল ।
শিল্প : সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীদের শিল্পবোধ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মৃৎশিল্পের কথা বলতে হয় । তারা কুমারের চাকার ব্যবহার জানত এবং তার সাহায্যে সুন্দর মাটির পাত্র বানাতে পারত । পাত্রগুলোর গায়ে অনেক সময় সুন্দর সুন্দর নকশা আঁকা থাকত । তাঁতিরা বয়নশিল্পে পারদর্শী ছিল । ধাতুর সাহায্যে আসবাবপত্র, অস্ত্র এবং অলঙ্কার তৈরি করা হতো । তারা তামা ও টিনের মিশ্রণে ব্রোঞ্জ তৈরি করতে শিখেছিল । কারিগররা রুপা, তামা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি দ্বারা তৈজসপত্র তৈরি করত । তাছাড়া সোনা, রুপা, তামা, ইলক্ট্রাম ও ব্রোঞ্জ ইত্যাদি ধাতুর অলঙ্কার তৈরিতে তারা পারদর্শী ছিল। অলঙ্কারের মধ্যে আংটি, বালা, নাকফুল, গলার হার, কানের দুল, বাজুবন্ধ ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য। সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীরা লোহার ব্যবহার জানত না। ধাতু ছাড়া দামি পাথরের সাহায্যে অলঙ্কার তৈরি করতেও তারা পারত । হাতির
দাঁতসহ অন্যান্য হস্তশিল্পেরও দক্ষ কারিগর ছিল । দলীয় কাজ : সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীরা যে যে শিল্পে পারদর্শী ছিল তার একটি তালিকা তৈরি কর ।
স্থাপত্য ও ভাস্কর্য : সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ এবং চমৎকার স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন রেখে গেছে । সেখানে দুই কক্ষ থেকে পঁচিশ কক্ষের বাড়ির সন্ধানও পাওয়া গেছে । আবার কোথাও দুই-তিন তলা ঘরের অস্তিত্ব আবিষ্কার হয়েছে। মহেঞ্জোদারোর স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো 'বৃহৎ মিলনায়তন' যা ৮০ ফুট জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছিল। তাছাড়া বিশাল এক প্রাসাদের সন্ধান পাওয়া গেছে । হরপ্পাতে বিরাট আকারের শস্যাগারও পাওয়া গেছে । মহেঞ্জোদারোতে একটি 'বৃহৎ স্নানাগার'-এর নিদর্শন পাওয়া গেছে যার মাঝখানে বিশাল চৌবাচ্চাটি ছিল সাঁতার কাটার উপযোগী ।
ভাস্কর্যশিল্পেও সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীদের দক্ষতা ছিল । পাথরে খোদিত ভাস্কর্যের সংখ্যা কম হলেও সেগুলোর শৈল্পিক ও কারিগরি দক্ষতা ছিল উল্লেখ করার মতো। এ যুগে মোট ১৩টি ভাস্কর্য মূর্তি পাওয়া গেছে। চুনাপাথরে তৈরি একটি মূর্তির মাথা পাওয়া গেছে । মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া গেছে নৃত্যরত একটি নারীমূর্তি। এছাড়া মাটির তৈরি ছোট ছোট মানুষ আর পশুমূর্তিও পাওয়া গেছে । হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম হলো বিভিন্ন ধরনের প্রায় ২৫০০ সিল । ধর্মীয় ও ব্যবসা- বাণিজ্যের প্রয়োজনে এগুলো ব্যবহৃত হতো ।
পটভূমি: গ্রিসের মহাকবি হোমারের 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্য দুটিতে বর্ণিত চমকপ্রদ কাহিনির মধ্যে লুকিয়ে থাকা সত্যকে খুঁজে বের করার অদম্য ইচ্ছা উৎসাহিত করে তোলে প্রত্নতত্ত্ববিদদের । উনিশ শতকের শেষে হোমারের কাহিনি আর কবিতায়ই তা সীমাবদ্ধ থাকে না, বেরিয়ে আসে এর ভিতরের সঠিক ইতিহাস । ইজিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জে এবং এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে আবিষ্কৃত হয় উন্নত এক প্রাচীন নগর সভ্যতা । সন্ধান মেলে মহাকাব্যের ট্রয় নগরীসহ একশ' নগরীর ধ্বংসস্তূপের। যাকে বলা হয় ইজিয়ান সভ্যতা বা প্রাক-ক্লাসিক্যাল গ্রিকসভ্যতা । ক্রিট দ্বীপ, গ্রিস উপদ্বীপের মূল ভূখণ্ড, এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে এবং ইজিয়ান সাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ নিয়ে গড়ে ওঠে এই সভ্যতা। এই সভ্যতার অধিবাসীরা ছিল সমৃদ্ধশালী সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের অধিকারী । এই সভ্যতাকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে । যথা-
১. মিনিয়ন সভ্যতা : ক্রিট দ্বীপে যে সভ্যতার উদ্ভব এর স্থায়িত্ব ধরা হয়েছে ৩০০০ থেকে ১৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত।
২. দ্বিতীয়টি হচ্ছে মাইসিনিয় বা ইজিয়ান সভ্যতা : গ্রিসের মূল ভূখণ্ডে দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত মাইসিনি নগরের নাম অনুসারে এর নামকরণ হয়। এই সভ্যতার স্থায়িত্ব ছিল ১৬০০ থেকে ১১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত । ধারণা করা হয় বন্যা অথবা বিদেশি আক্রমণের ফলে এই সভ্যতার অবসান ঘটে ।
ভৌগোলিক অবস্থান ও সময়কাল : গ্রিস দেশটি আড্রিয়াটিক সাগর, ভূমধ্যসাগর ও ইজিয়ান সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। গ্রিকসভ্যতার সঙ্গে দুইটি সংস্কৃতির নাম জড়িত । একটি ‘হেলেনিক' অপরটি ‘হেলেনিস্টিক’। গ্রিক উপদ্বীপের প্রধান শহর এথেন্সকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ‘হেলেনিক সংস্কৃতি' । অপরদিকে গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে মিশরের আলেজান্দ্রিয়াকে কেন্দ্র করে গ্রিক ও অ-গ্রিক সংস্কৃতির মিশ্রণে জন্ম হয় নতুন এক সংস্কৃতির । ইতিহাসে এ সংস্কৃতি ‘হেলেনিস্টিক সংস্কৃতি' নামে পরিচিত ।
সামরিক নগররাষ্ট্র স্পার্টা : প্রাচীন গ্রিসে যে অসংখ্য নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল তার একটি ছিল স্পার্টা । এ নগররাষ্ট্রের অবস্থান ছিল দক্ষিণ গ্রিসের পেলোপনেসাস নামক অঞ্চলে। অন্যান্য নগররাষ্ট্র থেকে স্পার্টা ছিল আলাদা । স্পার্টানদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমরতন্ত্র দ্বারা তারা প্রভাবিত ছিল । মানুষের মানবিক উন্নতির দিকে নজর না দিয়ে সামরিক শক্তি সঞ্চয়ের দিকে তাদের দৃষ্টি ছিল বেশি। ৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে দীর্ঘ যুদ্ধের পর ডোরিয় যোদ্ধারা স্পার্টা দখল করতে সক্ষম হয়েছিল । এই পরাজিত স্থানীয় অধিবাসীদের ভূমিদাস বা হেলট বলা হতো । এরা সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করত । পরাজিত অধিবাসী যারা ভূমিদাস হতে বাধ্য হয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। ফলে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা আর বিদ্রোহ দমন ছাড়া স্পার্টার রাজাদের মাথায় আর কোনো চিন্তা ছিল না । স্পার্টানদের জীবন স্পার্টা রক্ষার জন্যই নিয়োজিত ছিল । স্পার্টার সমাজ তৈরি হয়েছিল যুদ্ধের প্রয়োজনকে ঘিরে। সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের জন্য নাগরিকদের প্রস্তুত করা ও যুদ্ধ পরিচালনা করা । সামরিক দিকে অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ার কারণে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা ছিল অনগ্রসর ।
গণতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র এথেন্স : প্রাচীন গ্রিসে প্রথম গণতন্ত্রের সূচনা হয় এথেন্সে। তবে, প্রথম দিকে এথেন্সে ছিল রাজতন্ত্র । খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে এক ধরনের অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় । ক্ষমতা চলে আসে অভিজাতদের হাতে। দেশ শাসনের নামে তারা শুধু নিজের স্বার্থই দেখত। ফলে সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় । যদিও তাদের পক্ষে ক্ষমতা দখল করা সম্ভব হয়নি । কিন্তু তাদের নামে কিছু লোক ক্ষমতা হাতে নিয়ে নেয় । তাদের বলা হতো 'টাইরান্ট' । জনগণের মধ্যে অসন্তোষ এবং বঞ্চিত কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখা দেয়। ফলে সপ্তম খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মাঝামাঝি সময়ে রাষ্ট্রব্যবস্থায় এক পরিবর্তন আসে । আগে অভিজাত পরিবারের সন্তান অভিজাত বলে গণ্য হতো । এখন অর্থের মানদণ্ডে অভিজাত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলো ।
দেশে মারাত্মক সংকটের সময়ে সব শ্রেণি সর্বসম্মতভাবে কয়েকজনকে সংস্কারের জন্য আহ্বান জানায় । তার মধ্যে সবচেয়ে খ্যতিমান ছিলেন অভিজাত বংশে জন্ম নেয়া ‘সোলন' । তিনি কিছু নতুন আইন প্রণয়ন করেন এবং গ্রিক আইনের কঠোরতা হ্রাস করেন । তিনি ঋণ থেকে কৃষকদের মুক্ত করার জন্য আইন পাস করেন । তাঁর সময় অনেক অর্থনৈতিক সংস্কারও করা হয় । সোলনের পর জনগণের কল্যাণে তাদের অধিকার দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন পিসিসট্রেটাস এবং ক্লিসথেনিস । তারা জনগণের কল্যাণের জন্য অনেক আইন পাস করেন । তবে চূড়ান্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় পেরিক্লিসের সময়। তার সময়কে গ্রিকসভ্যতার ‘স্বর্ণযুগ' বলা হয়ে থাকে । ৪৬০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ক্ষমতায় এসে তিনি ৩০ বছর রাজত্ব করেন। তিনি নাগরিকদের সব রাজনৈতিক অধিকারের দাবি মেনে নেন ।
তিনি এ সময় প্রশাসন, আইন ও বিচার বিভাগে নাগরিকদের অবাধ অংশগ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। নাগরিকদের মধ্য থেকে নিযুক্ত জুরি বিচারের দায়িত্ব পালন করত । পেরিক্লিসের যুগে এথেন্স সর্বক্ষেত্রে উন্নতির শিখরে আরোহণ করে । ৪৩০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এথেন্সের ভয়াবহ মহামারিতে এক-চতুর্থাংশ লোক মৃত্যুবরণ করে । এই মহামারিতে পেরিক্লিসেরও মৃত্যু ঘটে । তাঁর মৃত্যুর পর পরই এথেন্সের দুর্ভোগ শুরু হয় ।
জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে বিশ্বসভ্যতায় অবিস্মরণীয় অবদান রাখা নগররাষ্ট্র এথেন্সের পতন হয় সামরিক নগররাষ্ট্র স্পার্টার কাছে । উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তা ইতিহাসে পেলোপনেসিয়ার যুদ্ধ নামে পরিচিত। ৪৬০ থেকে ৪০৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত মোট তিনবার এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় । এই যুদ্ধে দুই রাষ্ট্র পরস্পরের মিত্রদের নিয়ে জোট গঠন করে । এথেন্সের মিত্র রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত জোটের নাম ছিল ‘ডেলিয়ান লীগ'। অপরদিকে স্পার্টা তার মিত্রদের নিয়ে যে জোট গঠন করে, তার নাম ছিল ‘পেলোপনেসীয় লীগ” । এই মরণপণ যুদ্ধে এথেন্সের মান-মর্যাদা ও স্বাধীনতা বিলীন হয়ে যায় । ৩৬৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ এথেন্স চলে যায় স্পার্টার অধীনে । এরপর নগররাষ্ট্র থি অধিকার করে নেয় এথেন্স । ৩৩৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ মেসিডোনের (গ্রিস) রাজা ফিলিপ থিরাস দখল করে নিলে এথেন্স মেসিডোনের অধীনে চলে যায় ।
সভ্যতায় গ্রিসের অবদান: ভৌগোলিক কারণে গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলো একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেও তাদের সংস্কৃতি ছিল অভিন্ন । রাজনৈতিক অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও তারা একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বলে মনে করত । তাদের ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, খেলাধুলা – সবকিছু এক সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিল। এই সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূল অবদান ছিল এথেন্সের । আর এই সংস্কৃতির নাম হচ্ছে হেলেনীয় সংস্কৃতি ।
শিক্ষা : শিক্ষা সম্পর্কে গ্রিক জ্ঞানী-গুণীরা বিভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন । তারা নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন । তাদের কেউ কেউ মনে করতেন সুশিক্ষিত নাগরিকের হাতেই শাসনভার দেওয়া উচিত । সরকারের চাহিদা ও লক্ষ্য অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা থাকা উচিত। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল আনুগত্য ও শৃঙ্খলা শিক্ষা দেওয়া । স্বাধীন গ্রিসবাসীর ছেলেরা সাত বছর বয়স থেকে পাঠশালায় যাওয়া-আসা করত । ধনী ব্যক্তিদের ছেলেদের ১৮ বছর পর্যন্ত লেখাপড়া করতে হতো। কারিগর আর কৃষকের ছেলেরা প্রাথমিক শিক্ষা পেত। দাসদের সন্তানের জন্য বিদ্যালয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল । মেয়েরাও কোনো প্রতিষ্ঠানে গিয়ে লেখাপড়া করতে পারত না ।
সাহিত্য : সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রিসের সৃষ্টি আজও মানবসমাজে মূল্যবান সম্পদ। হোমারের ইলিয়াড’ ও ‘ওডিসি' মহাকাব্য তার অপূর্ব নিদর্শন। সাহিত্য ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল নাটক রচনায়। বিয়োগান্ত নাটক রচনায় গ্রিকরা বিশেষ পারদর্শী ছিল। এসকাইলাসকে এই ধরনের নাটকের জনক বলা হয় । তাঁর রচিত নাটকের নাম 'প্রমিথিউস বাউন্ড'। গ্রিসের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন সোফোক্লিস। তিনি একশ'টিরও বেশি নাটক রচনা করেন। তাঁর বিখ্যাত নাটকের মধ্যে রাজা ইডিপাস, আন্তিগোনে ও ইলেকট্রা অন্যতম। আর একজন বিখ্যাত নাট্যকারের নাম ইউরিপিদিস। এরিস্টোফেনেসের মিলনান্তক ও ব্যঙ্গ রচনায় বিশেষ খ্যাতি ছিল।
ইতিহাস রচনায়ও গ্রিকরা কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। হেরোডটাস ইতিহাসের জনক নামে পরিচিত ছিলেন। হেরোডটাস রচিত ইতিহাস-সংক্রান্ত প্রথম বইটি ছিল গ্রিস ও পারস্যের মধ্যে যুদ্ধ নিয়ে। থকিডাইডেস ছিলেন বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক। তাঁর বইটির শিরোনাম ছিল 'দ্য পেলোপনেসিয়ান ওয়র' ।
ধর্ম : গ্রিকদের বারোটি দেব-দেবী ছিল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পূজা ছাড়াও তারা বীরযোদ্ধাদের পূজা করত । জিউস ছিল দেবতাদের রাজা। অ্যাপোলো ছিলেন সূর্য দেবতা, পোসিডন ছিলেন সাগরের দেবতা। এথেনা ছিলেন জ্ঞানের দেবী । বারোজনের মধ্যে এই চারজন ছিলেন শ্রেষ্ঠ। রাষ্ট্রের নির্দেশে পুরোহিতরা ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতেন। ডেলোস দ্বীপে অবস্থিত ডেলফির মন্দিরে বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের মানুষ সমবেত হয়ে এক সঙ্গে অ্যাপোলো দেবতার পূজা করত।
দর্শন: দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে গ্রিসে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল । পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, প্রতিদিন কীভাবে এর পরিবর্তন ঘটছে—এসব ভাবতে গিয়ে গ্রিসে দর্শনচর্চার সূত্রপাত। থালেস ছিলেন প্রথম দিককার দার্শনিক। তিনিই প্রথম সূর্যগ্রহণের প্রাকৃতিক কারণ ব্যাখ্যা করেন। এরপর গ্রিসে যুক্তিবাদী দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের বলা হতো সফিস্ট। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু নেই। পেরিক্লিস তাঁদের অনুসারী ছিলেন। সক্রেটিস ছিলেন এ দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান । তার শিক্ষার মূল দিক ছিল আদর্শ রাষ্ট্র ও সৎ নাগরিক গড়ে তোলা । অন্যায় শাসনের প্রতিবাদ করার শিক্ষাও তিনি দেন। সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো গ্রিক দর্শনকে চরম উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটলও একজন বড় দার্শনিক ছিলেন ।
বিজ্ঞান : গ্রিকরা প্রথম বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত করে ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অঙ্কন করেন গ্রিক বিজ্ঞানীরা। তারাই প্রথম প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী একটি গ্রহ এবং তা নিজ কক্ষপথে আবর্তিত হয় । গ্রিক জ্যোতির্বিদরা সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ নির্ণয় করতে সক্ষম হন। চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। বস্ত্র ও বিদ্যুৎ জিউসের ক্রোধের কারণে নয়, প্রাকৃতিক কারণে ঘটে – এই সত্য তারাই প্রথম আবিষ্কার করেন। জ্যামিতির পণ্ডিত ইউক্লিড পদার্থবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। বিখ্যাত গণিতবিদ পিথাগোরাস ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিপোক্রেটসের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল ।
স্থাপত্য ও ভাস্কর্য : গ্রিক শিল্পের বিশেষ করে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। গ্রিক চিত্রশিল্পের নিদর্শন মৃৎপাত্রে আঁকা চিত্রের মধ্যে দেখা যায় । স্থাপত্যের সুন্দর সুন্দর নিদর্শন গ্রিসের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে । বড় বড় স্তম্ভের উপর তারা প্রাসাদ তৈরি করত । আর প্রাসাদের স্তম্ভগুলো থাকত অপূর্ব কারুকার্যখচিত । পার্থেনন মন্দির বা দেবী এথেনার মন্দির স্থাপত্য কীর্তির অন্যতম নিদর্শন। এথেন্সের অ্যাক্রোপলিসে স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শনের ভগ্নাবশেষ এখনও চোখে পড়ে । গ্রিক ভাস্কর্য পৃথিবীর শিল্পকলার ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগের জন্ম দিয়েছিল । সে যুগের প্রখ্যাত ভাস্কর্য শিল্পী ছিলেন মাইরন, ফিদিয়াস ও প্রাকসিটেলেস ।
খেলাধুলা : শিশুদের খেলাধুলার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হতো। বিদ্যালয়ে তাদের খেলাধুলার হাতেখড়ি হতো। শরীরচর্চা খেলাধুলার প্রতি গ্রিকদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। উৎসবের দিনে গ্রিসে নানা ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হতো। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল দেবতা জিউসের সম্মানে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতা । অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় গ্রিসের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদরা অংশ নিত। এতে দৌড়ঝাঁপ, মল্লযুদ্ধ, ঢাকা নিক্ষেপ, বর্শা ছোড়া, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকত । বিজয়ীদের জলপাই গাছের ডাল- পাতায় তৈরি মালা দিয়ে পুরস্কৃত করা হতো। প্রতি চার বছর পরপর এই খেলা অনুষ্ঠিত হতো। এ খেলায় বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের খেলোয়াড়রা অংশ নিত। এই খেলাকে ঘিরে গ্রিক নগররাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শত্রুতার বদলে সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব গড়ে ওঠে।
পটভূমি: গ্রিসের সভ্যতার অবসানের আগেই ইতালিতে টাইবার নদীর তীরে একটি বিশাল সম্রাজ্য ও সভ্যতা গড়ে ওঠে । রোমকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই সভ্যতা রোমান সভ্যতা নামে পরিচিত । প্রথম দিকে রোম একজন রাজার শাসনাধীন ছিল। এ সময় একটি সভা ও সিনেট ছিল । রাজা স্বৈরাচারী হয়ে উঠলে তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে ৫১০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ রোমে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় । রোমান সভ্যতা প্রায় ছয়শ' বছর স্থায়ী হয়েছিল ।
ভৌগোলিক অবস্থান ও সময়কাল: ইতালির মাঝামাঝি পশ্চিমাংশে রোম নগর অবস্থিত। ইতালির দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর থেকে উত্তর দিকে আল্পস পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত। ইতালি ও যুগোস্লাভিয়ার মাঝখানে আড্রিয়াটিক সাগর । আড্রিয়াটিক সাগর তীরে ইতালির উত্তর-পূর্ব অংশে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন সমুদ্রবন্দর এড্রিয়া । ইতালির পশ্চিমাংশেও ভূমধ্যসাগর অবস্থিত। সাগরের এ অংশকে প্রাচীনকালে বলা হতো এটুস্কান সাগর। কৃষি বিকাশের সুযোগ ছিল বলে প্রাচীন রোম ছিল কৃষিনির্ভর দেশ। ফলে রোমের আদি অধিবাসীদের সঙ্গে অনুপ্রবেশকারীদের সংঘর্ষ সাধারণ বিষয় ছিল । যে কারণে এসব সংঘাত-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে রোমানরা যোদ্ধা জাতিতে পরিণত হতে থাকে । রোমান ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নানা উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ৭৫৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রোম নগরী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান বর্বর জাতিগুলোর হাতে রোমান সম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন হয় ।
রোম নগরী ও রোমান শাসনের পরিচয় : গুরুত্বপূর্ণ টাইবার নদীর উৎসমুখ থেকে প্রায় বারো-তেরো মাইল দূরে সাতটি পর্বতশ্রেণির ওপর রোম অবস্থিত। এজন্য একে সাতটি পর্বতের নগরীও বলা হয়। ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর একদল মানুষ ইতালিতে বসবাস শুরু করে । তাদেরকেই লাতিন বলা হতো। তাঁদের নাম অনুসারে ভাষার নামও হয় লাতিন ভাষা । লাতিন রাজা রোমিউলাস রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন । তাঁর নাম অনুযায়ী নগরের নাম হয় রোম ।
রোমের গণতন্ত্র একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ধাপে ধাপে নানা সংস্কার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রোমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় । ঐতিহাসিকরা রোমান ইতিহাসকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন । যথা : ৭৫৩-৫১০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ছিল রাজতন্ত্রের যুগ। এ যুগে সাতজন সম্রাট দেশ শাসন করেন। এ যুগের সর্বশেষ সম্রাট টারকিউনিয়াস সুপারকাসকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর রোমে প্রজাতন্ত্রের সূত্রপাত হয়। এই প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চলে ৫০০ থেকে ৬০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত । রোমে প্রজাতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে জনগণ বিদ্রোহী নেতা ব্রুটাস এবং অপর এক ব্যক্তিকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে শাসনের সুযোগ প্রদান করে । রাজতন্ত্রের পতনের পর রোমের জনগণ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে, প্যাট্রিসিয়ান অর্থাৎ অভিজাত শ্রেণি, আর প্লিবিয়ান যারা সাধারণ নাগরিক । ক্ষুদ্র কৃষক, কারিগর, বণিকরা প্লিবিয়ান শ্রেণিভুক্ত ।
প্রজাতন্ত্রের প্রথম ২০০ বছর ছিল প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের মধ্যে সংঘাতের ইতিহাস । সমাজে প্লিবিয়ানরা বঞ্চিত শ্রেণি ছিল । অধিকারবঞ্চিত প্লিবিয়ানরা ক্রমাগত সংগ্রাম করতে থাকে । শেষ পর্যন্ত প্লিবিয়ানরা কিছু অধিকার আদায় করতে সক্ষম হয় । প্লিবিয়ানদের দাবির মুখে রোমান আইন সংকলিত হতে থাকে । ৪৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ প্লিবিয়ানরা ব্রোঞ্জপাতে ১২টি আইন লিখিতভাবে প্রণয়ন করে । আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয় হিসেবে দু'জন কনসালের মধ্যে একজন প্লিবিয়ানদের পক্ষ থেকে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এভাবে, রোমান প্রজাতন্ত্র গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হয় । রোমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও ক্রমে দেশটি সম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে । স্বল্প সময়ের মধ্যে রোম সমগ্র ইতালির ওপর প্রভাব বিস্তারে তৎপর হয়। ১৪৬ থেকে ৪৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রোমান সভ্যতার অন্ধকার যুগ । ধনী-দরিদ্র সংঘাত, দাস বিদ্রোহ, ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে চরম বিশৃঙ্খলা, হানাহানি, সহিংসতায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে রোম ।
রোমের অর্থনীতি ছিল দাসদের ওপর নির্ভরশীল । শাসকদের অমানুষিক নির্যাতনে দাসরা স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে । দুই বছরব্যাপী তারা তাদের বিদ্রোহ টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। ৭১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে স্পার্টাকাস নিহত হলে বিদ্রোহের অবসান হয় । চরম নির্যাতন নেমে আসে দাসদের ওপর । অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ছাড়াও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধেও জড়িয়ে পড়ে রোম । ফলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী সামরিক নেতারা ক্ষমতায় আসতে থাকেন এবং রোমে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে । ক্ষমতার দ্বন্দ্বের একপর্যায়ে সমঝোতার ভিত্তিতে তিনজন নেতা একযোগে ক্ষমতায় আসেন, যা ইতিহাসে ত্রয়ী শাসন নামে পরিচিত। বিশাল রোম সাম্রাজ্যকে তিন ভাগ করে শাসনের দায়িত্ব নেন অক্টেভিয়াস সিজার, মার্ক এন্টনি ও লেপিডাস । লেপিডাসের দায়িত্বে ছিল আফ্রিকার প্রদেশসমূহ, অক্টেভিয়াস সিজারের দায়িত্বে ছিল ইতালিসহ সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশ, এন্টনির দায়িত্বে ছিল পূর্বাঞ্চল । তবে তিনজনের শাসন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি । কারণ প্রত্যেকেরই আকাঙ্ক্ষা ছিল রোমের একচ্ছত্র অধিপতি বা সম্রাট হওয়ার ।
ফলে, খুব শীঘ্রই আবার ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়ে যায়। অক্টেভিয়াস সিজার পরাজিত করে লেপিডাসকে, এদিকে মার্ক এন্টনি মিশরের রাজকন্যা ক্লিওপেট্রাকে বিয়ে করে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করেন । কিন্তু অক্টেভিয়াস সিজারের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরাজিত হন । ক্ষমতা দখল করে অক্টেভিয়াস সিজার অগাস্টাস সিজার নাম ধারণ করে সিংহাসন আরোহণ করেন । ইতিহাসে তিনি এই নামেই বেশি পরিচিত । ১৪ খ্রিষ্টাব্দে অগাস্টাস সিজারের মৃত্যু হয় । তাঁর সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা যিশুখ্রিষ্টের জন্ম। অগাস্টাস সিজারের মৃত্যুর পর রোমে আবার বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় । বিদেশি আক্রমণ, বিশেষ করে জার্মান বর্বর গোত্রগুলোর আক্রমণ তীব্র হতে থাকে । তাছাড়া অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার কোন্দলের কারণে রোমানদের শক্তি ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে । রোমের শেষ সম্রাট রোমিউলাস অগাস্টুলাস জার্মান বর্বর গোত্রের তীব্র আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হলে ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটে। ইতোমধ্যে খ্রিষ্ট ধর্মের অগ্রযাত্রা শুরু হয় এবং জার্মানদের উত্থান ঘটে ।
সভ্যতায় রোমের অবদান : রোম শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য সর্বক্ষেত্রে গ্রিকদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল । তারা এসব বিষয়ে গ্রিকদের অনুসরণ ও অনুকরণ করেছে । তবে সামরিক সংগঠন, শাসন পরিচালনা, আইন ও প্রকৌশল বিদ্যায় তারা গ্রিক ও অন্যান্য জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল । এ ক্ষেত্রে আধুনিক বিশ্ব রোমানদের কাছে ব্যাপক ঋণী ।
শিক্ষা, সাহিত্য ও লিখন পদ্ধতি : এ সময়ে শিক্ষা বলতে বুঝাতো খেলাধুলা ও বীরদের স্মৃতিকথা বর্ণনা করা । যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে রোমের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সুতরাং তাদের সব কিছুই ছিল যুদ্ধকে কেন্দ্ৰ করে । তারপরও উচ্চ শ্রেণিভুক্ত রোমানদের গ্রিক ভাষা শিক্ষা ছিল একটি ফ্যাশন । ফলে এদের অনেকেই গ্রিক সাহিত্যকে লাতিন ভাষায় অনুবাদ করার দক্ষতা অর্জন করে । রোমের অভিজাত যুবকরা গ্রিসের বিভিন্ন বিখ্যাত বিদ্যাপীঠে শিক্ষালাভ করতে যেত । সে যুগে সাহিত্যে অবদানের জন্য প্লুটাস ও টেরেন্সর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা দু'জন মিলনাত্মক নাটক রচনার ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন । সাহিত্য ক্ষেত্রে সবচেয়ে উন্নতি দেখা যায় অগাস্টাস সিজারের সময় । এ যুগের কবি হোরাস ও ভার্জিল যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । ভার্জিলের মহাকাব্য 'ইনিড’ বহু ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে । ওভিদ ও লিভি এ যুগের খ্যাতনামা কবি । লিভি ইতিহাসবিদ হিসেবেও বিখ্যাত ছিলেন । বিখ্যাত ঐতিহাসিক ট্যাসিটাসও এ যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ।
স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও বিজ্ঞান: রোমান স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এর বিশালতা। সম্রাট হার্ডিয়ানের তৈরি ধর্মমন্দির প্যানথিয়ন রোমানদের স্থাপত্যের এক অসাধারণ নিদর্শন। ৮০ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সম্রাট টিটাস কর্তৃক নির্মিত কলোসিয়াম নাট্যশালা নির্মিত হয়, যেখানে একসঙ্গে ৫৬০০ দর্শক বসতে পারত। স্থাপত্যকলার পাশাপাশি রোমান ভাস্কর্যেরও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। রোমান ভাস্করগণ দেব-দেবী, সম্রাট, দৈত্য, পুরাণের বিভিন্ন চরিত্রের মূর্তি তৈরি করতেন মার্বেল পাথরের। বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হন। তাদের মধ্যে প্লিনি বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশ্বকোষ প্রণয়ন করেন। এতে প্রায় পাঁচশ বিজ্ঞানীর গবেষণাকর্ম স্থান পেয়েছে। তাছাড়া চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোমানদের অবদান ছিল। বিজ্ঞানী সেলসাস চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর বই লেখেন। এছাড়া চিকিৎসাশাস্ত্রে গ্যালেন রুফাসে অসামান্য অবদান রেখেছেন।
ধর্ম, দর্শন ও আইন : রোমানরা ধর্মীয় ক্ষেত্রেও গ্রিকদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। অনেক গ্রিক দেব-দেবীর নাম পরিবর্তন হয়ে রোমানদের দেব-দেবী হয়েছে । রোমানদের অন্যতম প্রধান দেবতার নাম ছিল জুপিটার। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দেব-দেবী হচ্ছে জুনো, নেপচুন, মাস, ভলকান, ভেনাস, মিনার্ভা, ব্যাকাস ইত্যাদি। রোমান দেবমন্দিরে প্রধান পুরোহিত ছিলেন যাঁরা, তাঁরা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন । তবে রোমানদের পরকালের প্রতি বিশ্বাস ছিল না। অগাস্টাস সিজারের সময় থেকে ঈশ্বর হিসেবে সম্রাটকে পূজা করার রীতি চালু হয়। উল্লেখ্য, এ সময় খ্রিষ্টধর্মের প্রবর্তক যিশুখ্রিষ্টের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে রোমান ধর্মের পাশাপাশি খ্রিষ্টধর্ম বিস্তার লাভ করতে থাকে। অনেক রোমান এই ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। এতে সম্রাট ক্ষুব্ধ হন কারণ খ্রিষ্টধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে গেলে সম্রাটকে আর ঈশ্বরের মতো পূজা করা যায় না। ফলে রোমান সম্রাটরা এই ধর্ম প্রচার বন্ধ করে দেন এবং খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণকারী রোমানদের ওপর নির্যাতন শুরু করেন। কিন্তু সম্রাট কন্সটানটাইন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং এই ধর্মকে রোমান সরকারি ধর্মে পরিণত করেন ।
অনেকে মনে করেন যে, রোমীয় দর্শন গ্রিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। তবুও রোমান দর্শনে সিসেরো লুক্রেটিয়াস (খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ৯৮-৫৫) তাঁদের সুচিন্তিত দার্শনিক মতবাদ দ্বারা অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন । রোমে স্টোইকবাদী দর্শন যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। ১৪০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ রোডস দ্বীপের প্যানেটিয়াস এই মতবাদ রোমে প্রথম প্রচার করেন।
বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে রোমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে আইন প্রণয়ন। খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রোমানরা ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনগুলো সুষ্ঠুভাবে একসঙ্গে সাজাতে সক্ষম হন। ৫৪০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ১২টি ব্রোঞ্জ পাতে সর্বপ্রথম আইনগুলো খোদাই করে লিখিত হয় এবং জনগণকে দেখাবার জন্য প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়। রোমান আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান । রোমান আইনকে তিনটি শাখায় ভাগ করা হয়েছে। যেমন—
১. বেসামরিক আইন : এই আইন পালন করা রোমান নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। এই আইন লিখিত অলিখিত দুই রকম ছিল ।
২. জনগণের আইন : এ আইন সকল নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য ছিল । তাছাড়া ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার বিষয়টি এই আইনে ছিল। তবে এর মাধ্যমে দাসপ্রথাও স্বীকৃতি লাভ করে । সিসেরো এ আইনের প্রণেতা ।
৩. প্রাকৃতিক আইন : এ আইনে মূলত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার কথা বলা হয়েছে । আধুনিক বিশ্ব সম্পূর্ণভাবে রোমান আইনের ওপর নির্ভরশীল। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে সম্রাট জাস্টিনিয়ান প্রথম সমস্ত রোমান আইনের সংগ্রহ ও সংকলন প্রকাশ করেন ।